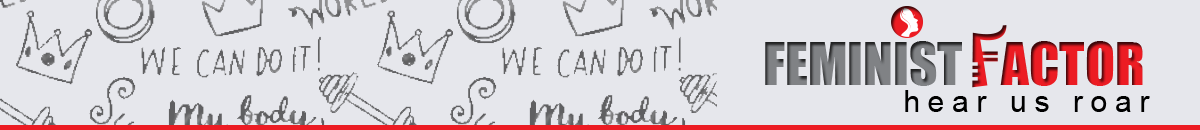৭১’র যৌন সহিংসতা: ট্রাইব্যুনালে কবে আলাদা গুরুত্ব পাবে?
পৃথিবীর ইতিহাস বলে, সব রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে নারী ও শিশু সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু যুদ্ধ থেমে যাবার পর তাদের প্রতিই দেখানো হয় সবচেয়ে বেশি অবহেলা, এমনকি ধর্ষণের শাস্তিও হয়নি অধিকাংশ ক্ষেত্রে। বিশ্বজুড়ে নানা সময়ে যুদ্ধে নারীর প্রতি যৌন সহিংসতার ঘটনা, যুদ্ধের পর এর বিচার, অপরাধের গুরুত্ব ও ঐতিহাসিক অবস্থান নিয়ে গবেষক হাসান মোরশেদের তিন পর্বের ধারাবাহিক ফেমিনিস্ট ফ্যাক্টরের জন্য।
আজ পড়ুন এর শেষ পর্ব।।
১৯৭১’র ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর- ২৬৬ দিনব্যাপী চলমান পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তাদের সহযোগীদের নৃশংসতার অন্যতম অনুষঙ্গ ছিল বাঙালি নারীদের ব্যাপক হারে ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতন।
তারা নারীদের উপর যৌন নির্যাতন চালায় তিনটি পর্যায়ে। স্পট রেপ- কোন গ্রাম/ শহর দখল করে সাথে সাথে ধর্ষণ করেছে। দখলকৃত কোন এলাকা এক বা একাধিক বাড়ির নারীদের তাদের ইচ্ছেমত যখন খুশি ধর্ষণ করেছে, তাদের ক্যাম্প/ বাংকারগুলোতে নারীদের যৌনদাসী হিসাবে রেখে দিয়েছে। এদের কাউকে কাউকে গর্ভবতী হবার পর একটা নির্দিষ্ট সময় পর ছেড়েছে যাতে গর্ভের সন্তান নষ্ট করতে না পারেন, অনেককে বিকৃত উপায়ে নির্যাতন করে মেরে ফেলেছে। পাকিস্তান আর্মিদের পরাজিত করে তাদের বাংকার থেকে বহু ধর্ষণের শিকার নারীকে উদ্ধার করেছেন মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় সৈনিকেরা।
পাকিস্তানি জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা তার বই A Stranger in my own country’তে লিখেছেন, জেনারেল নিয়াজী বাঙ্গালী সামরিক অফিসারদের সামনেই বলতো- ‘Main iss haramzadi qomki nasal badal doonga (I will change the race of the Bengalis)
হামদুর রহমান কমিশনে সাক্ষ্য দেয়া একজন পাকিস্তানি অফিসার বলেছেন- সেনাপতি নিজেই যেখানে ধর্ষক সেখানে সাধারণ সৈনিকদের আটকানো সম্ভব ছিল না।
যুদ্ধকালীন পাকিস্তানের মওলানারা ফতোয়া জারি করে যে মুক্তিযোদ্ধারা হিন্দু, এদেরকে হত্যা করা এবং তাদের নারীদের ‘গনিমতের মাল’ হিসাবে গ্রহণ করা জায়েজ। তাদের বিশ্বাস ছিল- প্রকৃত মুসলমান তার পিতার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় না। তাই ‘কাফের’ হিন্দু ও ‘নিচু জাত’ এর মুসলমান নারীদের ধর্ষণ করে তাদের গর্ভে ‘প্রকৃত বিশ্বস্ত মুসলমান’ জন্ম দেয়া তাদের ঈমানী দায়িত্ব।
আমেরিকাভিত্তিক ‘উইমেন মিডিয়া সেন্টার’ রিপোর্ট প্রকাশ করে পাকিস্তানি আর্মি ক্যাম্পগুলোতে ৮ বছরের শিশু থেকে ৭৫ বছর বয়স্কা নারী পর্যন্ত বন্দী ছিলেন। গণধর্ষণ প্রায় সময়ই গণহত্যায় রূপ নিতো। ক্যাম্পগুলো থেকে উদ্ধার হওয়া নারীদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে তারা এই রিপোর্ট পেশ করেছিলো।
বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ ধর্ষণের শিকার নারীর সংখ্যা দুই লক্ষ দাবি করে। তবে আমেরিকান লেখক ও সাংবাদিক সুসান ব্রাউনমিলার তাঁর বই ‘Against our will’ গ্রন্থে এই সংখ্যা চার লক্ষ উল্লেখ করেছেন। সুসান আরো জানিয়েছেন- আর্মি ক্যাম্পগুলোতে পর্ণ মুভি দেখিয়ে সৈনিকদের ধর্ষণে উৎসাহিত করা হত বলে তিনি সাক্ষ্য পেয়েছেন। স্বাধীনতার পর পর অস্ট্রেলিয়ান ডাক্তার জিওফ্রে ডেভিসকে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছিলো ধর্ষণের শিকার নারীদের গর্ভপাতের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারকে সহায়তা করার জন্য। ডেভিস ও তার অভিজ্ঞতা থেকে জানিয়েছেন- ধর্ষণের শিকার নারীর সংখ্যা চার লাখ হতে পারে।
সংখ্যা যাই হোক, এটা নিশ্চিত যে- এই ধর্ষণগুলো স্রেফ যৌন তাড়নাজনিত ছিল না, বরং বাঙালির জাতি পরিচয় বদলে দেবার উদ্দেশ্যেই পাকিস্তানের সামরিক নীতি নির্ধারকদের যুদ্ধের কৌশলের অংশ ছিল।
ধর্ষণ, নারীর প্রতি যৌন সহিংসতাকে জেনোসাইড কনভেনশনে আলাদাভাবে অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করা না হলেও রাফায়েল লেমকিন তার জেনোসাইড আলোচনায় খুব গুরুত্ব দিয়ে এই বিষয়টি উল্লেখ করেছিলেন। তিনি স্পষ্টভাবেই মতপ্রকাশ করেছিলেন- এসব ক্ষেত্রে নারীরা সহিংসতার শিকার হয় জাতিগত/ ধর্মীয়/নৃতাত্ত্বিক/ গোত্রগত পরিচয়ের কারণেই। নারীকে আক্রমণের মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর ‘অহং’কে যেমন আঘাত করা হয় তেমনি জনগোষ্ঠীর জৈবিক পরিচয় বদলে দেয়ার চেষ্টা করা হয়। নারীর প্রতি যৌন সহিংসতা হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোন ঘটনা নয়, সামগ্রিক পরিকল্পনার অংশ।
১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সৈনিকেরা বাঙালি নারীদের ধর্ষণ করেছে- তাদের গর্ভে ‘সাচ্চা মুসলমান’ জন্ম দেয়ার উদ্দেশ্যে, যারা ‘মহান পাকিস্তান’ জাতির অংশ হবে। রুয়ান্ডা ট্রাইব্যুনাল খুব গুরুত্ব সহকারে যৌন সহিংসতাকে বিবেচনা করেছে এবং জেনোসাইড হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে এর বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করেছে। যুগোশ্লাভিয়া ট্রাইব্যুনাল ধর্ষণকে ‘নির্যাতন’ এবং ‘যৌনদাসত্বের উদ্দেশ্যে আটক’কে মানবতাবিরোধী অপরাধ বলে অভিহিত করেছে।
৭১’র ধর্ষণ ও যৌন সহিংসতা প্রসঙ্গে বাংলাদেশে প্রচলিত ন্যারেটিভ হচ্ছে ‘দু লক্ষ মা বোনের ইজ্জত’ যা খুবই বাজে এবং অপ্রাসঙ্গিক ট্যাগিং। ধর্ষণের সাথে নারীর ইজ্জত/ সম্ভ্রমহানির কোন সম্পর্ক নেই। ধর্ষণ হচ্ছে নারীর বিরুদ্ধে পরিচালিত সহিংসতা- যা অপরাধ। অন্য কোন শব্দ প্রয়োগে সেই অপরাধকে আড়াল করা হয়।
আরেকটি বিষয় খেয়াল করা যায়, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির সুযোগে ধর্ষণ বেড়ে গেলে অনেকেই মন্তব্য করেন- ৭১ এর বিভীষিকাকে ছাড়িয়ে গেছে’। খেয়াল রাখা জরুরি, ৭১ এর ধর্ষণ ছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সামগ্রিক পরিকল্পনার অংশ, জাতিগোষ্ঠীর বায়োলজিক্যাল ধরণ বদলে দেবার জন্য। এর গুরুত্ব ও প্রতিক্রিয়া সংখ্যা দিয়ে পরিমাপযোগ্য নয়।
মুক্তিযুদ্ধ শেষে নির্যাতিত নারীদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি চিরাচরিত ছিলো, একটা রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ সমাজ মানসকে খুব বদলে দিয়েছিলো- অন্ততঃ নারীর প্রতি সহানুভূতিশীল করেছিলো তেমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায়না। অনেক নারীই নিজ নিজ পরিবার কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হন।
তবে যুদ্ধবিধ্বস্ত কাঠামো ও শূন্য রিজার্ভ নিয়ে যাত্রা শুরু করা রাষ্ট্র এই নারীদের প্রতি দায়িত্বশীল ছিলো। সে সময় অতি দ্রুত ৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়ে নারী পুনর্বাসন কেন্দ্র গঠন করা হয়- মহকুমা পর্যায় পর্যন্ত কেন্দ্রের শাখা বিস্তৃত হয়। নির্যাতিত নারীদের এসব কেন্দ্রে নিয়ে আসা হয় তাদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের জন্য। রেডক্রসের সহায়তায় বিদেশি চিকিৎসকরা আসেন, অনেক নারীর গর্ভপাত করানো হয়, যাদের গর্ভপাত সম্ভব ছিল না- তাদের সন্তান প্রসব হয়, এই সন্তানদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ইউরোপ ও কানাডায় দত্তক দেয়া হয়। এই পর্যায়ের পর নির্যাতিত নারীরা হস্ত, কুটির শিল্প ও সেলাই প্রশিক্ষণ নিতে থাকেন তাদের আর্থিক স্বনির্ভরতার উদ্দেশ্যে।
এর পাশাপাশি বাংলাদেশ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অক্সিলারী ফোর্স জামাতে ইসলামীকে নিষিদ্ধ করে। সাথে সব ধরণের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ এবং জামাতে ইসলাম প্রধান গোলাম আজমসহ পালিয়ে যাওয়া অনেক যুদ্ধাপরাধীর নাগরিকত্বও বাতিল করে বাংলাদেশ সরকার। বাঙালি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য ১৯৭২সালের ২৪ জানুয়ারি দ্যা বাংলাদেশ কোলাবরেটরস (স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল) অর্ডার, ১৯৭২ (ইংরেজি: “The Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Order, 1972”)- প্রনয়ন করা হয় যা দালাল আইন নামে পরিচিত। এই আইনে মুক্তিযুদ্ধের সময় সংগঠিত ধর্ষণকে গুরুতর অপরাধ হিসাবে গন্য করা হয়।
১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি আইনটির আদেশ জারি হলেও পরবর্তীকালে একই বছরের ৬ ফেব্রুয়ারি, ১ জুন এবং ২৯ আগস্ট তারিখে তিন দফা সংশোধনীর মাধ্যমে আইনটি চূড়ান্ত হয়। এর পাশাপাশি সরকারি চাকরিতে কর্মরতদের কেউ দালালি এবং যুদ্ধাপরাধের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কি না তা যাচাই করার জন্য ১৯৭২ সালের ১৩ জুন একটি আদেশ জারি করে যা তখন গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়।
পরবর্তীতে দালাল আইনের অধীনে ৩৭ হাজারের বেশি ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাদের দ্রুত বিচারের জন্য সরকার সারা দেশে ৭৩টি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে। ৭৩-এর অক্টোবর পর্যন্ত দুই হাজার ৮৮৪টি মামলা নিষ্পত্তি হয়। ৭৫২ জনের সাজাও হয়। এদের মধ্যে কয়েকজনের মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল। বাকিদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড থেকে শুরু করে বিভিন্ন মেয়াদে দণ্ড হয়েছিল।
এ সময় বর্ষিয়ান রাজনীতিবিদ মওলানা ভাসানীসহ অনেকেই দালাল আইন বাতিলের জন্য সরকারকে চাপ দেন।
১৯৭৩ সালের ৩০ নভেম্বর দালাল আইনে আটক যেসব ব্যক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ নেই তাদের জন্য ক্ষমা ঘোষণা করা হয়। এ ঘোষণার পর দালাল আইনে আটক ৩৭ হাজারের অধিক ব্যক্তির ভেতর থেকে প্রায় ২৬ হাজার ছাড়া পায়।
সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হলেও যে কয়টি অপরাধের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষমার আওতাভুক্ত করা হয়নি ধর্ষণের অভিযোগ তার মধ্যে অন্যতম। ক্ষমার আওতাভুক্ত নয় এরকম ১১ হাজার অপরাধীর বিচার তখনও চলছিল- এদের মধ্যে ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্তও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক থাকার কথা।
কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর দৃশ্যপট দ্রুত বদলে যায়। ঐ বছরের ৩১ ডিসেম্বর দালাল আইন বাতিল করা হয়। অবশিষ্ট ১১ হাজারকে কারাগার থেকে মুক্ত করা হয় এবং সামরিক সরকারের তত্ত্বাবধানে এদেরকে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে পুনর্বাসিত করা হয়। এসব পুনর্বাসিতদের কতজনের বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলা ছিল সেই উপাত্ত অবশ্য কেউ সংগ্রহ করেননি, তবে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়।
২০০৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে ক্ষমতায় এসে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য ‘আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল’ গঠন করে। প্রবল জনমতের চাপে এটি তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল এবং ধারণা করা হয় বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্ম এই প্রতিশ্রুতির কারণেই ২০০৮ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়। প্রধান বিরোধী দল বিএনপিসহ দেশ ও দেশের বাইরের প্রভাবশালী কিছু গোষ্ঠীর বিরোধিতার শিকার হয়েও আইসিটি-বিডি তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত ৭০ এর অধিক মামলার রায় ঘোষিত হয়েছে- শীর্ষ যুদ্ধাপরাধীদের অনেকের ফাঁসীর রায় হয়েছে, আরো অনেকগুলো মামলা তদন্ত পর্যায়ে আছে।
জেনোসাইড, মানবতাবিরোধী অপরাধ, যুদ্ধাপরাধসহ সবগুলো আন্তর্জাতিক অপরাধের বিচারের এখতিয়ার ট্রাইব্যুনালের থাকলেও বেশির ভাগ মামলার রায়ে মানবতাবিরোধী অপরাধের উপর জোর দেয়া হয়েছে। বিচারকদের বিশ্লেষণে জেনোসাইড বিষয়টি উল্লেখ হলেও সুনির্দিষ্টভাবে জেনোসাইডের অপরাধে কোন রায় ঘোষিত হয়নি এখনো। অন্যান্য অপরাধের সাথে ‘নারীর বিরুদ্ধে যৌন সহিংসতা’ অপরাধে রায় ঘোষিত হয়েছে অন্তত দুটি, ময়মনসিংহের আলবদর কমান্ডার রিয়াজউদ্দীন ফকির ও হবিগঞ্জের সৈয়দ কায়সার। দুজনের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত।
তবে ‘নারীর বিরুদ্ধে যৌন সহিংসতা’কে ট্রাইব্যুনালে অধিকতর গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার জন্য রুয়ান্ডা ও বসনিয়ার নারী অধিকার কর্মীরা ( নুসরেতা সিভাক এর নাম প্রণিধানযোগ্য) যে জনমত গঠন করেছিলেন, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সেরকম কিছু দৃশ্যমান ছিল না, এখনো নেই। নির্যাতিত নারীদের উল্লেখযোগ্য অংশ প্রান্তিক পর্যায়ের, চার যুগ পেরিয়ে তারা বয়স ভারাক্রান্ত। সাক্ষ্য দেয়ার জন্য যে মানসিক প্রস্তুতি, সাক্ষ্য দিতে গিয়ে যে ট্রমা, সাক্ষ্য দেয়ার পর সামাজিক নিরাপত্তা- এই পর্যায়গুলোতে উল্লেখযোগ্যভাবে তাদের পাশে কেউ দাঁড়ায়নি।
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে ‘নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা’কে আরো গুরুত্বপুর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ নিতে বাংলাদেশের নারী ও মানবাধিকার কর্মীরা কেন আগ্রহী হননি- সেটা একটা বিস্ময় এবং ভবিষ্যত অনুসন্ধানের বিষয় হিসাবে থেকে যাবে।
প্রথম পর্ব- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যৌনসহিংসতা, কমফোর্ট উওম্যানের কান্না
দ্বিতীয় পর্ব- রুয়ান্ডা ও বসনিয়া যুদ্ধের নৃশংস যৌন নির্যাতন এবং শাস্তি