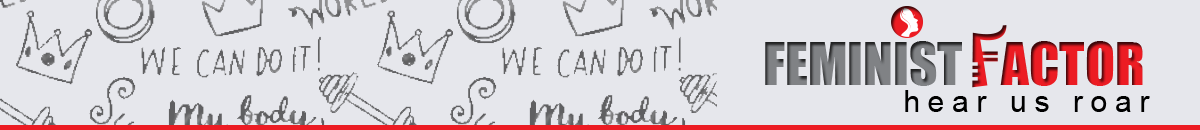আদিবাসীদের প্রতি বাঙালির সংকীর্ণতা: মনের চোখ খুলবে কবে?
আবরার শাহ্।। প্রথমেই বলে রাখি, সিনেমা বিষয়ে আমি বোদ্ধা কেউ নই। সমালোচক, বিশ্লেষক তো নই-ই। বড়জোর মনোযোগী দর্শক। তদুপরি স্বল্পদৈর্ঘ্যের সিনেমা আমি কমই দেখি, কেননা যে ক’টি স্বল্প দৈর্ঘ্যের দেশীয় সিনেমা দেখেছি বেশিরভাগই আমার ভালো লাগে নি। সিংহভাগই মনে হয়েছে গল্প দুর্বল, চিত্রনাট্য অপরিপক্ক, অভিনয় একেবারে কাঁচা, ‘পরিচালক’ তকমা লাগানোর বালখিল্য রোমান্স, নেহায়েত ভাঁড়ামো কিংবা ‘শক্তিশালী’ কোনো বার্তা দিকে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে তালকানা দশা!
তবে এই মুভিটি তার ব্যতিক্রম। উপরে যে-সব পয়েন্ট পাওয়া গেছে, তার সব ক’টিই বরং এই মুভির শক্তির জায়গা।সাথে চমৎকার আবহ সংগীত, শুরুর দিকে মাদল ব্যান্ডের একটি প্রতিবাদী গানের গিটারের সুর এবং শেষের দিকে দারুণ জনপ্রিয় একটা চাকমা সংগীতের ব্যবহার যেন আক্ষরিক অর্থেই কানের আরাম।
মাঝে মধ্যে অপ্রাসঙ্গিকভাবে ধান ভানতে শিবের গীতও গাওয়া লাগে ঘটনার ঘনঘটায়। একটু নিজের কথায় ফিরি তবে।
দাদুর বাড়ি লামা হওয়ার কারণে ছেলেবেলায় বিচ্ছিন্ন তবে সুখকর কিছু সময় কেটেছে সেই ছোট্ট পাহাড়ি গ্রাম অংহ্লা পাড়া আর লামায়। তবে দুখজাগানিয়া হলো, একটা চরম নাড়িছেঁড়া টান অনুভব করা সত্ত্বেও ধারাবাহিকভাবে একটানা কখনোই আমার সেখানে থাকা হয় নি। কারণ দাদুবাড়ি যেখানটায় সেখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল অনেক দূরে আর বাবার আয় রোজগারের উৎস ছিল চকরিয়া কিংবা কক্সবাজারকেন্দ্রিক এবং কখনো চট্টগ্রাম বা ঢাকা বা সারাদেশ। ফলশ্রুতিতে চকরিয়াতেই আপাত সেটেল্ড হওয়া আর স্কুল জীবনটা হস্টেলের বদ্ধ দেয়ালে কাটাতে বাধ্য হওয়া। তবে স্পষ্টভাবেই মনে পড়ে খুব উদগ্রীব হয়ে বসে থাকতাম কখন দাদু বাড়িতে বেড়াতে যাব সে আশায়। অনেকবার বাবাকে দাদু বাড়িতে নিয়ে যেতে বিরক্ত করায় মারও খেয়েছি! ছোটবেলায় চকরিয়াতে কোরবানির ইদের সময় দেখতাম লামা থেকে ম্রু বা মুরং সম্প্রদায়ের মানুষজন কোরবানির এক-দুই দিন আগেই এলাকায় এসে পূর্ব পরিচিত মানুষদের বাড়িতে আশ্রয় নিতো গরুর ভুঁড়ির আশায়। এলাকার বাচ্চাদের দেখতাম তাদের পিছনে সারাক্ষণ ঘুরঘুর করতে, গোল হয়ে অবাক নয়নে তাদের দিকে চেয়ে থাকতে। বাচ্চাদের দোষ ছিল না, তারা কখনো স্বগোত্রের, স্বচেহারার মানুষ ছাড়া ভিন্নধর্মী কাউকে দেখে অনভ্যস্ত। তবে এলাকার মাঝবয়েসী কিংবা বুড়োদের কাউকে কাউকে দেখতাম মুরংদের ভাষা, পরিচ্ছদ, চুল বাঁধার স্টাইল নিয়ে মজা নিতে কিংবা খারাপ ব্যবহার করতে যা আমাকে কষ্ট দিতো।
বড় হওয়ার পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম, অনেক কিছু বুঝতে শিখলাম, সবার সাথে যোগাযোগ বাড়লো, মেলামেশা বাড়লো, ঘনিষ্ঠভাবে সারাদেশের সব জাতি-সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে হৃদ্যতা তৈরি হওয়ার একটা সুযোগ হলো। বাঙালি বন্ধু-বান্ধবদের অনেককেই দেখতাম পাহাড়ি আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের নিয়ে মজা নিতে, সঠিক বাংলা উচ্চারণ করতে না পারা নিয়ে পাশ থেকে হাসি ঠাট্টা করতে! অথচ তারা তখন বেমালুম ভুলে যেতো যে পাহাড়িদের মাতৃভাষা বাংলা নয়, এটি তাদের কাছে নেহাতই একটি বিদেশি ভাষার তুল্য। অন্যদিকে ছোটকাল থেকে তখন অবধি ইংরেজি ভাষা শিখে আসা বন্ধুদের অনেকেরই দু-লাইন ইংরেজি বলতেই পা কাঁপত!
অতি উৎসাহী কেউ তো উত্তেজিত হয়ে বলেই ফেলতো যে এদেশে থাকতে হলে নাকি সঠিক উচ্চারণে বাংলা বলতে হবে! দেশটা যেন তাদের বাপের নামে নামজারি করা! অথচ চট্টগ্রামের অধিকাংশ মানুষই সঠিক ও শুদ্ধ বাংলায় (চলিত বাংলা!) কথা বলতে পারে না!
কেউ-কেউ আবার পাহাড়িদের দেশপ্রেম নিয়েও প্রশ্ন তুলতো। পাহাড়ের সংঘাতের সিকিভাগ ভেজালযুক্ত ঘটনা জেনে ঢালাওভাবে সবাইকে দেশদ্রোহী গাদ্দার আখ্যা দিতো। ১৯৭১ সালে চাকমা রাজার পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন এবং রাজার অনুসারী কিছু চাকমা মানুষের মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী অবস্থান এবং সরাসরি মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে জোর গলায় তুলে ধরতো। বেমক্কা ভুলে যেতো মূল স্রোতের বাঙালিদের অনেকেরও রাজাকার, শান্তি বাহিনীর ক্যাড়ার হয়ে বিপথগামী হওয়ার আখ্যান। ভুলে যেতো বিখ্যাত চাকমা মুক্তিযোদ্ধা মেজর মনি স্বপন দেওয়ানের কথা, একমাত্র পাহাড়ি বীর বিক্রম ইউকে চিং এর কথা,মং রাজা মং প্রু সাইনের কথা যিনি মানিকছড়িস্থ উনার রাজবাড়ী মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য শুধু উন্মুক্তই করে দেন নি, নিজের লাইসেন্স করা বন্দুক তুলে দিয়েছিলেন তাদের হাতে, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন, এমনকি নিজে অস্ত্র হাতে সম্মুখযুদ্ধে অংশ নিয়ে আর্মির অনারারি অফিসার হয়েছিলেন। আর সে অপরাধেই উনার ঐতিহ্যবাহী, ঐশ্বর্যপূর্ণ রাজবাড়ী পাকি সৈনরা পুড়িয়ে দিয়েছিল।ভুলে যেতো সেই অভাগী চাইন্দাও মারমাসহ শত শত পাহাড়ি বীরাঙ্গনাদের কথা যুদ্ধের পর যাদের পরিবার ও সমাজ গ্রহণ করে নি। ভুলে যেতো হাজার হাজার পাহাড়ি আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানের কথা।
অথচ দেশপ্রেম একটি সহজাত বিষয়, এটা জোর করে কাউকে গেলানো যায় না কিংবা কেড়েও নেওয়া যায় না। যে ভূমিতে মানুষ জন্মায়, বেড়ে ওঠে, যে পতাকাকে ছোটবেলা থেকে স্কুলের অ্যাসেমব্লিতে স্যালুট দেয়, যে জাতীয় সংগীত সম্মিলিত কণ্ঠে গেয়ে গেয়ে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে সেসব পবিত্র অনুভূতি মনের অগোচরেই দেশপ্রেম হয়ে অনুরণিত হয় নাগরিকের মনে ও মননে। দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন তোলা, অযাচিত জ্ঞান দেয়া যেন নিজের মা’কেই ভালোবাসাতে শেখানো। এর চেয়ে ছোটলোকি, নির্লজ্জ, বিবেকহীন কাজ আর হতে পারে না। এসব আচরণ একজনের মানসলোকে, মনস্তত্বে কী ভয়াবহ খারাপ প্রভাব ফেলে তাও সংখ্যাগুরুরা কখনো ভাবেন নি কিংবা ভাবার দরকারই বোধ করেন নি হয়তো। সবচেয়ে লজ্জাজনক ও আফসোসের বিষয় হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের মত সর্বোচ্চ জ্ঞানোন্মেষের জায়গায় পড়েও বেশির ভাগেরই কূপমণ্ডূক হওয়া, মানসিক সংকীর্ণতা অতিক্রম করতে না পারা, সবাইকে সাথে নিয়ে এক হয়ে চলার মত উদার হতে না পারা, সর্বোপরি ধর্ম-জাতের সংকীর্ণ দেয়াল অতিক্রম করে মানুষ হিসেবে ভাবতে পারার মতো মহৎ গুণাবলির সন্নিবেশ না ঘটা।
‘৯৭ সালে পাহাড়ে শান্তির বার্তাবাহী শান্তি চুক্তি হলেও কার্যত তা অশান্তির ঘেরাটোপেই বন্দী। বিশেষত ভূমি সমস্যার সমাধান না হওয়া,অভিবাসী সমতলের বাঙালিদের বিষয়ে কার্যকর সিদ্ধান্তে না আসা, বাঙালি ও পাহাড়িদের মধ্যকার অবিশ্বাস ও সন্দেহ নিরসনে কার্যকর নাগরিক সংলাপ বা ভ্রাতৃত্ববোধ বাড়ানোর কোন ফলপ্রসূ পদক্ষেপ না নেওয়া, ভারত প্রত্যাগত অভ্যন্তরীন উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে না পারা, চুক্তি মোতাবেক “অপারেশন উত্তরণ” বন্ধ না হওয়া, স্থায়ী সেনানিবাস ব্যাতীত বাকি সেনা ক্যাম্প বা অস্থায়ী সেনা চৌকি না সরানো কার্যত শান্তি চুক্তিটিকেই শান্তিহীনতার পথে কয়েক ধাপ এগিয়ে দিয়েছে।
তবে সরকার পক্ষের সাথে সাথে বিবাদমান গ্রুপগুলোর কয়েকটি পক্ষেরও চুক্তির মৌলিক ধারাগুলো বাস্তবায়নে অনীহা, উদাসীনতা তাদের সশস্ত্র আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তিকেও প্রশ্নের মুখে ঠেলে দেয়।

শেষ কথা: কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়াদের স্বল্প দৈর্ঘ্যের সিনামিটি দেখা অবশ্য কর্তব্য। এতেও যদি অচলায়তন ভেঙে কারো কারো মানস চক্ষু দিশা পায় তবে সেটাই পাওয়া। জাতিগত বা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বুকচেরা কষ্ট যদি কিছুটা হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠরা বুঝতে পারে, সহমর্মী, সমব্যথী হয় তবে হয়ত একদিন শান্তি, সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্বের সুবাতাস বইবে বাংলাবান্ধা থেকে ছেঁড়া দ্বীপ, মনাকশা থেকে আখাইনঠংয়ে।
[ফেমিনিস্ট ফ্যাক্টরে প্রকাশিত মুক্তমত লেখকের নিজস্ব বক্তব্য]