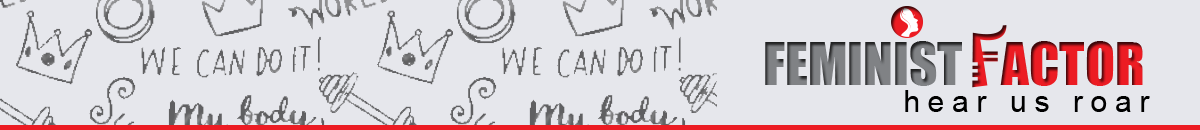পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রভুত্ব অস্বীকার করুক নারী
চেন রাখাইন।। ভিক্টিম ব্লেমিং- অদ্ভুত এক ধরনের প্রবণতা দেখা যায় আমাদের সমাজে। এই ভিক্টিম ব্লেমিং-এর অন্যতম শিকার নারী। কোনো ঘটনায় যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কোনো এক অদ্ভুত কারণে সেই ক্ষতিগ্রস্ত মানুষটাকেই দোষী সাব্যস্ত করাকে ভিক্টিম ব্লেমিং বলা হয়। যেমন— কোনো মেয়ে যখন ধর্ষণের শিকার হয়, তখন অনেকে ঘুরে ফিরে মেয়েটাকেই দোষ দিতে উঠে পড়ে লাগে, মেয়েটার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলা শুরু করে, মেয়েটা রাতে বের হল কেন সেটা নিয়ে তদন্ত কমিটি গঠনের দাবি তোলে, মেয়েটার পোশাক কেমন ছিল সেটা নিয়ে নানা কেচ্ছা-কাহিনী বানানো শুরু করে দেয়। তাই শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, ভিক্টিম মেয়েটা একটা বিপজ্জনক অবস্থায় পড়ে যায়। যেখানে মানুষ তার সাথে ঘটা অন্যায়-অনাচারের বিরুদ্ধে কথা বলবে, অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার দাবি তুলবে, সেখানে দেখা যায়, সেই ভিক্টিম মেয়েটাকে দোষারোপ করে নানা মিথ্যা রটনা করা হয় এবং সেগুলো ডালপালা মেলে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এইভাবে নারীরা ভিক্টিম ব্লেমিং-এর শিকার হন। এমন ঘটনার পর ভিক্টিম নিরুপায় হয়ে নির্বাক হয়ে যান। অনেকে আবার অভিমানে জীবনের মায়া সাঙ্গ করে পরপারে পাড়ি জমান।
নারীরা সমাজে বেড়ে ওঠে শাসন-শোষণের মাধ্যমে; ভিক্টিম হয়ে। একটা ছেলে তেমন কোনো ঝামেলা ছাড়াই বড় হয়। ছেলে বলে সে স্কুলে গেলে তাকে কেউ টিজ করে না, বাইরে ঘুরতে গেলে বকা শুনতে হয় না। কিন্তু মেয়েদের পথ এত সোজা না। মেয়েদের পাড়ি দিতে হয় কণ্টকাকীর্ণ পথ। স্কুল-কলেজে গেলে তাকে ইভটিজিং-এর শিকার হতে হয় এবং মেয়েটি যদি ‘কেউ তাকে উত্ত্যক্ত করে’ এমন অভিযোগ পরিবারে করে, তখন অনেক রক্ষণশীল পরিবার সেটার সমাধান না করে উল্টো মেয়েটির স্কুল-কলেজে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। যদি মেয়েটি ধর্ষণের শিকার হয়, এলাকাবাসী ধর্ষকের শাস্তি দাবি না করে বিভিন্ন অপবাদ দিয়ে মেয়েটাকে নষ্টা হিসেবে উপস্থাপন করতে শুরু করে এবং দুর্বিষহ করে তোলে মেয়েটির জীবন, লাঞ্ছিত করে মাটিতে মিশিয়ে দেয় তার পরিবারকে। উদ্ভট সব প্রশ্ন করে ভিক্টিম মেয়েটাকে দোষী বানানোর প্রাণান্তকর অপচেষ্টা করা হয়; আর তার সাথে ঘটা জঘন্য অন্যায়কে বিভিন্নভাবে জাস্টিফাই করার চেষ্টা করা হয়। মেয়েরা সামাজিকভাবে এই পরিস্থিতিগুলোর মধ্য দিয়ে বড় হয় বলে তারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে ভয় পায়, নিপীড়িত জীবনকে ঈশ্বরপ্রদত্ত মনে করে। এভাবেই তারা শেষ পর্যন্ত অবিচারের বেড়াজালে আটকে পড়ে অসহনীয় যন্ত্রণা বুকে চেপে বন্দীশিবিরে নির্বাসিত থেকে কাটিয়ে দেয় পুরো জীবন।
শহরে তুলনামূলক একটু কম হলেও গ্রামে উল্লিখিত ঘটনাগুলো ঘটে নিয়মিত, আরো ভয়ংকরভাবে। কোনো মেয়ে এবং তার পরিবার এই ধরণের কোনো অন্যায়ের শিকার হলে এই ব্যাপারে মুখই খুলতে চায় না আত্মসম্মানের(!) কথা ভেবে! আমি বুঝি না আসলে এমন আত্মসম্মানের কী মূল্য থাকতে পারে! পরিবারের বদনাম হবে ভেবে তারা নীরবে অন্যায় সয়ে যায়। কিন্তু তারা এটা ভুলে যায় যে, অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে তারা উভয়ই সমান অপরাধী। ঢালাওভাবে তাদের দোষ দেওয়াও আসলে ঠিক না। আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজটা এভাবেই গড়ে উঠেছে। এখানে নারীকে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক মনে করা হয়। নারীদের পুরুষের চাইতে নিম্নশ্রেণির মনে করা হয়। সমাজ ঠিক করে দেয় মেয়েদের বৈশিষ্ট্য কেমন হবে বা হতে পারবে; আর কেমন হতে পারবে না। যেমন – মেয়েদের বেশি লেখাপড়া করার দরকার নেই; তাদের তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দিতে হবে; শান্তশিষ্ট হতে হবে; চঞ্চল হতে পারবে না; অন্যায়-অবিচার মুখ বুঁজে সহ্য করতে হবে ইত্যাদি। তাদের মনস্তত্ত্বে এইসব অসাম্যের বিষ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়; নিজেদের স্বাধীন মানুষ ভাবতে নিরুৎসাহিত করা হয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ এইভাবে নারীদের শোষণের পথ তৈরি করেছে।
পুরোপুরি নাহলেও এখন সমাজের চিত্র অনেকখানি বদলেছে; বদলেছে মানুষের চিন্তা-ভাবনা। মেয়েরা আর আগের মতো সামাজিক অযৌক্তিক শোষণ মেনে নেয় না। এদের পথ প্রশস্ত করে দিয়ে গেছেন যারা, তারা হচ্ছেন, স্রোতের বিপরীতে চলা সেই মানুষগুলো, যারা তাদের জীবন বিপন্ন করে লড়াই করে গেছেন। তাদের আন্দোলন, প্রতিবাদের ফল হচ্ছে আজকের এই সমাজ। যদিও এখনো পথ পুরোপুরি উন্মুক্ত হয়নি। তবুও আজকে মেয়েরাও যে ছেলেদের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে, রাজনীতি-অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারছে, ঠিকভাবে লেখাপড়া করার সুযোগ পাচ্ছে; এসব কিছুই বেগম রোকেয়াদের মত কিছু সাহসী নারীদের অবদানের ফসল। তারা যদি সেসময় শোষিত থেকে ঘরবন্দী থেকে দাসত্ব মেনে নিতেন, তাহলে আজকে আমরা এই নারীজাগরণ দেখতে পেতাম না। যদি মেয়েদের ক্লাস ফোর পর্যন্ত পড়তে দেওয়া হতো, পর্দার অন্তরালে অবরোধবাসিনী করে রাখা হতো, তাহলে আমরা নারীদের অবদান কোথাও খুঁজে পেতাম না। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের মধ্যযুগীয় চিন্তা-ভাবনা মেয়েদের অনেক পিছিয়ে দিয়েছে। মেয়েরা যখন তাদের এই চিন্তার শিকার হয়ে পিছিয়ে পড়ে, তখন আবার তারাই মেয়েদের ‘পিছিয়ে পড়া’কে প্রাকৃতিক দাবি করে মেয়েদের মেধাকে অবমূল্যায়ন করে এবং মেয়েদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করে বসে। ব্যাপারটা খুবই হাস্যকর।
সেই মানব সভ্যটার সূচনালগ্ন থেকে, অর্থাৎ যেটা ‘হান্টিং অ্যান্ড গ্যাদারিং সোসাইটি’ নামে পরিচিত এবং কার্ল মার্ক্স যাকে আদিম সাম্যবাদী সমাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন, সে সময় থেকে মেয়েদের জীবনের বিবর্তনের ধারাটা খেয়াল করলে বোঝা যায় তাদের পুরুষের নিকট অধীনস্থ থাকার কারণ; বোঝা যায় তাদের অনগ্রসরতার পেছনের রহস্য। তখনকার সমাজে ছেলেরা শিকার করতো আর মেয়েরা ফলমূল সংগ্রহ করতো। এনার্জেটিক কাজ সব ছেলেরা করতো। মেয়েদের করতে দেওয়া হতো অপেক্ষাকৃত কম শক্তি লাগে এমন কাজ। তাই ছেলেরা শারীরিকভাবে একটু শক্তিশালী হয়ে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বেড়ে উঠেছে। অন্যদিকে মেয়েরা একটু দুর্বল হয়ে বেড়েছে। মেয়েদের যেহেতু সন্তান ধারণ করতে হয়, তাই মেয়েদের অনেকসময় কেটে যেত সন্তান গর্ভধারণে ও সন্তান লালন-পালন করতে করতে; আর পুরুষেদের যেহেতু এসবের ঝামেলা নেই, তাই তাদের সেই বাড়তি সময় বিভিন্ন সৃজনশীল কাজে লাগাতে পারতো। তাই তারা জ্ঞানবিজ্ঞানে, নিত্যনতুন জিনিস আবিষ্কারে বেশি অবদান রাখার সুযোগ পেত। তাই বিবর্তনের দিক থেকে চিন্তা করলে মেয়েদের শারীরিকভাবে দুর্বল হওয়াটা এবং একটু পিছিয়ে থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। এইজন্য হুমায়ূন আজাদের একটা কথা খুব প্রাসঙ্গিক এখানে। তিনি বলেছিলেন—
“পুরুষতান্ত্রিক সমাজে শ্রেষ্ঠ শহীদের নাম হচ্ছে মা।”
কিন্তু আধুনিক সভ্য সমাজে এটা প্রমাণিত সত্য যে, মেয়েরাও সমান সুযোগ পেলে পুরুষের সমকক্ষ হতে পারে। তারাও জ্ঞানবিজ্ঞানের সব শাখায় বিচরণ করতে পারে সমান দক্ষতায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখনো তাদের শারীরিক দুর্বলতা দেখে কেউ কেউ নারীদের তুলনায় পুরুষেরা শ্রেষ্ঠ এমন দাবি তোলে এবং অধিকাংশ মেয়েও নিজেদের পুরুষের তুলনায় কম মেধাসম্পন্ন মনে করে। এদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে ইচ্ছা করে মাদাম ম্যারিকুরির দিকে, স্মরণ করিয়ে দিতে ইচ্ছে করে হাইপেশিয়ার কথা। ম্যারিকুরি একজন বিশ্ব বিখ্যাত নারী বিজ্ঞানী; যিনি কি-না দুই দুইটা নোবেল পুরস্কার বিজয়ী, তাও আবার পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞানের মত পিওর সাইন্সে! হাইপেশিয়ার ছিলেন একজন তুখোড় গণিতবিদ ও দার্শনিক।
আসল কথা হচ্ছে, কেউ কারো থেকে শ্রেষ্ঠ না। সবাই যার যার জায়গায় অনন্য। আমরা বরাবরই খুব প্রতিযোগী মানসিকতার হয়ে থাকি। আমরা সবাই নিজেদের শ্রেষ্ঠ দাবি করতে পছন্দ করি। আমার দেশ শ্রেষ্ঠ, আমার ধর্ম শ্রেষ্ঠ, আমার ভাষা শ্রেষ্ঠ, আমার সংস্কৃতি শ্রেষ্ঠ, আমার স্কুল-কলেজ শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি। এইরকম চিন্তাকে ‘উগ্র জাতীয়তাবাদী’ চিন্তা বলা হয়। এই জাতীয়তাবাদী চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে হিটলার ও তার নাৎসি বাহিনী ষাট লক্ষ ইহুদি হত্যা করেছিল। শ্রেষ্ঠত্বের দাবি নিয়ে আমরা বারবার একে অপরের সাথে অপ্রয়োজনীয় সংঘাতে জড়িয়ে পড়ি। যদিও এখানে সংঘাতের কোন প্রয়োজনীয়তাই নেই। নারী-পুরুষ একে অপরের প্রতিযোগী না, বরং সহযোগী এবং পরিপূরক।
মেধার উৎকৃষ্টতা কখনো লিঙ্গ দ্বারা নির্ধারিত হয় না। যে যত বেশি পরিশ্রম করবে, মস্তিষ্ক ব্যবহার করবে, সুযোগ-সুবিধা পাবে সে তত ভাল কিছু করতে পারবে। মেধা কখনো লিঙ্গভিত্তিক, বর্ণভিত্তিক, ধর্মভিত্তিক হয় না। জন্মসূত্রে পাওয়া কোনোকিছু নিয়ে কাউকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা উচিত না, নিপীড়ন করা ঠিক না। জন্মসূত্রে যদি কেউ মেয়ে-ছেলে, কালো-ফর্সা, লম্বা-বেঁটে, হিন্দু-মুসলিম, প্রতিবন্ধী হয়, তাহলে সেটা নিয়ে তাকে ছোট করা যায় না। কারণ সে এগুলো নিজে বেছে নেয় নি, নিজে অর্জন করেনি। তাই মেয়ে বলে কাউকে কম মেধাসম্পন্ন প্রচার করে শোষণকে বৈধতা দেওয়া, পুরুষ বলে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করা অনৈতিক।
সভ্যতাকে এগিয়ে নিতে গেলে জ্ঞানবিজ্ঞানে, রাজনীতি-অর্থনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ অতি প্রয়োজনীয়। মোট জনসংখ্যার অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে ঘরবন্দি রেখে আসলে খুব বেশি উন্নতি করা যায় না। তাই পুরুষের উচিত নারীদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করা। শোষক হয়ে নয়, বরং সহযোগী হয়ে পাশে থাকা। পথের কাঁটা হয়ে না থেকে, পথের সাথী হয়ে পাশে থাকা। যদি পুরুষ ও নারী পরস্পরের সহযোগী হয়ে চলে তাহলে একদিন সভ্যতার পথে পথে, ইতিহাসের পাতায় পাতায় পুরুষের সাথে নারীর নামও পাওয়া যাবে। কবির মতো আমিও সেই অনাগত দিনের জন্য তীর্থের কাকের মতো অপেক্ষা করে আছি— যেদিন ধরণী পুরুষের সাথে নারীর জয়গানও গাইবে।
কিন্তু দীর্ঘদিন শোষিত হয়ে বেড়ে ওঠার কারণে নারীদের মধ্যেও এক ধরণের মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘটেছে। এর ফলে, তারা শোষণকে স্বাভাবিক বলেও মেনে নিয়েছে। এমন ধ্যান-ধারণাই আসলে তাদের প্রধান শত্রু। তারা ধরে নিয়েছে তারা যেহেতু নারী, তাই তাদের পুরুষের প্রভুত্ব মেনে নিয়েই বেঁচে থাকতে হবে। “যারা পুরুষের অনুগত হয়ে চলে তারাই ভাল মেয়ে”, “কোনো কারণেই পুরুষের বিরুদ্ধাচরণ করা যাবে না, ভাল মেয়েরা এমনটি করে না” — এমন কিছু কথা তাদের মনে প্রোগ্রাম করে দেওয়া হয়। নিজেদের স্বাধীন সত্তা হিসেবে তাই তারা আর মনেই করে না। তাই একটু অধিকার পেলে তারা ভেবে বসে, যেন তারা সাত রাজার ধন পেয়েছে! এজন্য বর্তমানে আমরা তাদের খুশি হয়ে বলতে শুনি— আমাকে আমার হাজবেন্ড চাকরি করতে দেয়, বাইরে যেতে দেয়- এমন সব কথা। এই সমস্ত কথা শুনলে আমার হাসি পায়। চাকরি করতে দেয় মানে কী? কেউ চাকরি করবে কি করবে না, সেটা তো অন্য কেউ ঠিক করে দিতে পারে না। এটা তার ব্যক্তিগত অধিকার। স্বাধীন, স্বনির্ভর মানুষ কখনো অন্যের ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হয় না; আর অন্য কারো ওপর কর্তৃত্ব আরোপও করে না। স্বামী-স্ত্রী হিসেবে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু কেউ কারো ব্যক্তিগত অধিকার জোর করে কেড়ে নিতে পারে না। কারো কোনো মত ‘সম্পর্কের মূলা’ দেখিয়ে অন্যের ওপর চাপিয়ে দিতে পারে না। মানসিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যাওয়ার কারণে সমাজে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের নানা অনাচার-অবিচারের শিকার হতে হয়। তারা যতদিন না স্বনির্ভর, স্বাধীন সত্তার অধিকারী হবে, ততদিন তাদের শোষিত হয়ে বেঁচে থাকতে হবে। বেঁচে থাকতে হবে ভিক্টিম হয়ে, জীবনযাপন করতে হবে ভিক্টিম ব্লেমিং এর শিকার হয়ে; আজীবন কাটাতে হবে এই বিষাদের অভয়ারণ্যে। তাই বিদ্রোহী কবি তাদের আহবান করেছেন এইভাবে—
“চোখে চোখে আজ চাহিতে পারো না; হাতে রুলি, পায়ে মল
মাথায় ঘোমটা, ছিঁড়ে ফেলো নারী, ভেঙে ফেলো ও-শিকল
যে-ঘোমটা তোমা করিয়াছে ভিরু ওড়াও সে আবরণ!
দূর করে দাও দাসীর চিহ্ন ঐ যত আভরণ!”
[ফেমিনিস্ট ফ্যাক্টরে প্রকাশিত মুক্তমত লেখকের নিজস্ব বক্তব্য]