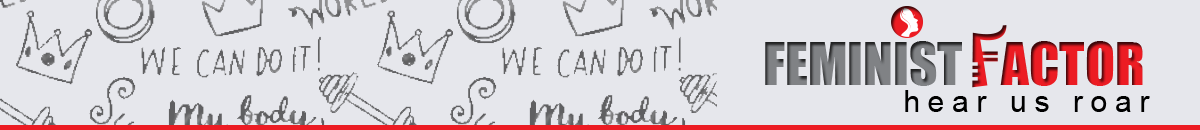দিদিমা’র মৃত্যুদিন এবং পিতৃতন্ত্রের সাথে পরিচয়ের প্রথম পর্ব
অপর্ণা হাওলাদার ।। লিখতে গিয়ে দেখলাম, সহজ নয় এইসব অভিজ্ঞতা শব্দে ধারণ করা। মৃত্যুই নাকি জন্মের পর একমাত্র সত্য, কিন্তু কিছু কিছু মৃত্যু কোনো কোনো জীবনকে সংযোগহীন করে ফেলে। কিছু কিছু মৃত্যু জীবিত মানুষের চেয়ে বড় শক্তি হয়ে পাশে থাকে। তখন হয়তো মৃত্যু যা দেয় তা শোক নয়, এইসব অভিজ্ঞতা আনে দীর্ঘমেয়াদী বিষাদ। কে আমি কিংবা আমি কেন জন্ম নিলাম এইরকম গভীর প্রশ্নের মতো। ততটা কি পূর্ণ মানুষ আমি, কিংবা হবো কোনোদিন যাতে জন্মের ঋণ শোধ হয়? স্বগতকথনের মত মৃত্যু ছায়া হয়ে থাকে, সাথে সাথে।
প্রথম মৃতদেহ দেখা আমার ১৯৯৫ সালে। এর আগে বরিশালে আত্মীয়, প্রতিবেশী কারো মৃত্যুর পর সামনে গিয়ে দেখা হয়নি, বা দেখতে দেওয়া হয়নি। ক্লাস ফোরে আমি যখন একা ঢাকায় থাকি, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ব্যাচেলর্স কোয়ার্টারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষক মারা যান। তিনি অবিবাহিত ছিলেন, একাই থাকতেন। সকালে ওনার মৃতদেহ যখন নিয়ে যাওয়া হয়, সেই আমার দেখা প্রথম মৃতদেহ। উনি শান্ত মানুষ ছিলেন, ব্রহ্মচারী ধরণের যে আইডিয়া থাকে বই-এ! ওনার মৃতদেহ দেখেও আমার ঘুমন্ত একজন শান্ত মানুষ মনে হয়। নাকে তুলো দেওয়া ছিলো, যদি পার্থক্য ধরতেই হয়। মরে গেলে কি সবাইকেই শান্ত লাগে?
আজকে লিখছি আমার দিদিমা’র (নানী) মৃত্যুদিন নিয়ে। এই দিনটা এত বছর পরেও এত স্পষ্ট! আমার নানাবাড়ি বরিশালে। আমি ক্লাস থ্রি পর্যন্ত বরিশালেই থাকতাম, এরপর ঢাকায় আসি। এর কিছুদিন পর দিদিমা’র গল্ডব্লাডারে অপারেশন করতে হবে বলে ঢাকায় আসেন। ভদ্রমহিলার একটা অদ্ভুত শান্ত, সমাহিত ভাব ছিল। অপারেশন তাকে বেশি একটা ভাঙ্গেনি। কিন্তু রাতে তার পাশে শোয়ার পর, একথা ধীরে বলেছিলেন, তোর রুমটা কেমন বলিস তো। তোদের নতুন বাসা তো আর আমার হয়তো দেখা হবে না। দেখা হবে না – মানে কি, আমি জানতাম না।
ঢাকায় এসে অপারেশনের সময় ধরা পরে ক্যান্সার অনেকখানি ছড়িয়ে পড়েছে। সেটা আমার ক্লাস ফাইভের প্রথম দিকে। দিদিমা’কে জানানো হয়নি যে তার ক্যান্সার। এটা বোধকরি আমাদের সমাজের রোগীর ট্রিটমেন্টের একটা বড় গলদ। এরপর দিদিমা, মা বরিশালে চলে যায়; আমি আবার ঢাকায় থাকি। ডাক্তার সমীর মামা’র বাসা থেকে দিদিমা যেদিন বরিশালে যান, সেদিন কি দিদিমা’র সাথে আমার শেষ কথা? আমার শেষ কথা কবে হয়েছিলো তার সাথে, আমি মনে করতে পারি না। আমরা কী নিয়ে কথা বলেছিলাম?
এর কয়েকদিন পর আমার ছোটো মাসি বরিশালে আসেন কলকাতা থেকে, সেই সময়েও কয়েকদিনের জন্য আমি বরিশালে যাই। কিন্তু প্রায় ১৫ বছর পর বরিশালে মাসি আসায়, সবাই ব্যস্ত ছিল। হৈ হল্লা আমারও ভালো লাগে না, বিশেষত আমার প্রবল পুরুষতান্ত্রিক কাজিন ভাইদের মেয়েদের নিয়ে মন্তব্যে আমি প্রচণ্ড বিরক্ত হই। আমার বোন অনেক ছোট, আমি একাই তাদের টার্গেট। এত ভিড়ের মধ্যে আমার দিদিমা’র সাথে কথা হয় না।
ক্লাস ফাইভের শেষের দিকে আমরা ব্যাচেলর্স কোয়ার্টার ছেড়ে ঈশা খান রোডে আসি। ২১ বছর এর শিক্ষকতা জীবন শেষে আমার বাবা’র তখন একরুমের স্টুডিও থেকে দুই বেডরুমের বাসায় যাওয়া। ঈশা খান রোডের বাসা বড়, কিন্ত পুরনো ধাঁচের বাসাগুলো। দেয়ালের, দরজার অবস্থা প্রায় জঘন্য। কিন্তু আমার প্রথম নিজের রুম। নিজের রুম ব্যাপারটা ভিন্ন স্বাদের, একটা আলাদা স্বাধীনতা। রুমের পাশেই বাথরুম, অ্যাটাচড না যদিও। এই বাসায় ট্রান্সফারের কাজ চলার মধ্যেই দিদিমা’র অবস্থা ডেটেরয়েট করে। ক্যান্সার ধরা পড়ার পর রেডিওথেরাপি, কেমোথেরাপি নেওয়ার মত শরীর তাঁর ছিল না। কিন্তু ঢাকায় থাকায় আমি জানতাম না এইসব। শরীর খারাপ, সবাই চিন্তিত, এটুকু জানতাম।
বরিশালে গেলাম আমরা ডিসেম্বরের কোনোদিন, ঠিকঠাক মনে পড়ে, ভেতরের ঘরে ঢুকে দেখি একটা মানুষ বিছানায় শোয়া। অক্সিজেন দেওয়া। সে নড়তে-চড়তে পারে না। তার শরীরে পচন ধরে বলে পরিষ্কার করতে হয়। তার খাবার নল দিয়ে ঢোকে। তার কাউকে চেনার, দেখার, কিছু শোনার ক্ষমতা নেই। এই দৃশ্য দেখার জন্য বা অনুধাবন করার জন্য মানসিক প্রস্তুতি আমার ছিল না। লাইফ সাপোর্টে কাউকে কেনই বা বাঁচিয়ে রাখে মানুষ? যেতে দিলেই হয়, অনেক তো হলো কষ্ট করা। এই বেঁচে থাকা নিজের জন্য নয়, অন্যের সান্তনার জন্য কেবল। দিদিমা বিছানাবন্দী অবস্থাতেই শেষের দিকে আমার বড় মাসি আসেন তার দুই মেয়ে নিয়ে। এদের কাউকেও আমি দেখিনি। বাসায় এত মানুষ, এত হইচই। হয়তো এই ভিড়ই সবাইকে প্রস্তুত করে ধাক্কা সামলানোর জন্য। এই বাড়ি বড় বেশি এই ভদ্রমহিলাকেন্দ্রিক তো।
১৩ই জানুয়ারি, আসলে সন্ধ্যা থেকেই একটা অদ্ভুত নির্জনতা ছিল। হয়তো সবাই প্রতীক্ষা করছিল। রাত ১২ টার পর, ১৪ই জানুয়ারি, এইসব কষ্টের হাত থেকে সাধনা বটব্যাল মুক্তি পান। গভীর রাত, কিন্তু বাড়িভর্তি লোক। পাশের দুই-তিন বাড়ির সবাই চলে এসেছে। মৃত্যু কী, যেমন বললাম, আমার ধারণা নেই। আমি, আমার স্বভাবমত, মানুষ দেখি; আর কে কী করে, কেন করে, কীভাবে করে। এই যে প্রায় ৮ মাসের ক্যান্সারপরবর্তী জীবন দিদিমা’র, এর মধ্যে দাদুকে জানানো হয়নি যে দিদিমা’র ক্যান্সার। বলা হয়েছিলো, অসুস্থ, ঠিক হয়ে যাবে। এই মারা যাওয়ার পর রাতে ততক্ষণে দাদু ঘুমিয়ে পড়েছিলেন হয়তো। হইচই এ উঠে গেছেন। তাঁর পাশে বসে মামা বলেন যে দিদিমা’র ক্যান্সার ছিলো। আমি দাদুর দিকে আগ্রহ নিয়ে চেয়ে দেখি। দাদু’র কি চোখে জল? উনি বলেন কিছু ধীরে ধীরে, “তোরা আমাকে আগে বলতি। আমি একটু ভালো ব্যবহার করতাম তোর মায়ের সাথে কয়দিন”।
এই কথা আজ ২৩ বছর পরেও আমি স্পষ্ট শুনতে পাই। একজন বিদ্বান লোক, সারাজীবন ইংরেজি অংক পড়িয়েছেন মিশনারি স্কুলে। পুরুষতন্ত্র তাকে একটা বিশাল অস্ত্র হাতে তুলে পাঠিয়েছে দুনিয়ায়, তিনি তাঁর উজ্জ্বল, প্রতিভাবান, প্রচণ্ড ধীরস্থির কিন্তু দৃঢ মনের স্ত্রী’র মৃতদেহ পাশের রুমে রেখে প্রথম বলেন, “আমি একটু ভালো ব্যবহার করতাম!”
সারা বাড়িতে সারারাত ধরে হা হুতাশ কান্নাকাটি চললো। মানুষের চিৎকার করে কান্না দেখে আমার শুধু কৌতুহল জাগে কেন একেক মানুষ একেকভাবে কাঁদে? আমি, সাধনা বটব্যালের বহু যত্নে তৈরি করা প্রায়-আঁতেল একটি ক্রিয়েচার, তাঁরই মৃত্যুতে একেক রুমে ঘুরে ঘুরে মানুষের শুয়ে-বসে-দাঁড়িয়ে কান্নাকাটি অনেক মনোযোগ দিয়ে দেখি। পর্যবেক্ষণ করি আসলে। আমার মা কারণে অকারণে অনেকই কাঁদেন, সুতরাং তাঁর কান্না আমাকে তেমন আকৃষ্ট করে না। পাশের বাসার এক মেয়ে দরজায় হাত ঠেকিয়ে হাহাকার করছিল, আমি এটা দেখি। কিন্তু যা আমাকে সত্যিকার অর্থেই টানে, সে হলো মামা। মামা দিদিমা’র চেয়ে গুণে গুণে সতের বছরের ছোটো। মামা পানের একটা ডাটা মুখে দিয়ে সব সামলে চলার চেষ্টা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যান। কিন্তু মামা কাঁদেন না, অন্য সবাইকে তদারকি করেন। মরলেও তো শান্তি নেই, মরাবাড়ির লোকের সহস্র কাজ। সকালে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার জন্য দিদিমা’কে প্রস্তুত করা হয়।
মৃত শরীরে সাদা শাড়িতে চিকন রঙিন পার পরানো হয়, সে এই সাজেই থাকতো। এই সাজে তাকে ভালো লাগে দেখতে। খাটিয়ায় আনা হয় সধবার বেশে, কপালে সিঁদুর হাতে শাখা। মহিলারা বলাবলি করেন, আহা কী ভাগ্য। সধবাই মরেছেন। আহা যেন, দাদু আগে মারা গেলে কী না কী হয়ে যেতো। আগেই বলেছি, মৃত্যু আমাকে বিচলিত করে না। মৃত্যু মানে কি, তাই আমি জানি না। এই যে খাটিয়া তোলা হবে, তারপর এই জীবনে ওই মুখ আমি আর দেখবো না, পৃথিবীর যে কোনো মানুষে – অল্প স্নেহের স্বরেই খুঁজে যাবো শুধু, সেই কথা সেইদিন অত স্পষ্ট ছিল না। আমি দাদুকে দেখি। তাকে আটকে রাখা হয়েছে আসলে দূরে, পাশের বাসার বেবি মাসির প্রহরায়। দাদু ভুলভাল বকেন সেইদিন। প্রবল পুরুষ তিনি, তাঁর শরীরে প্রাবল্য একরাতেই উধাও। খাটিয়ায় তোলার আগে আগে, পানের ডাটা মুখে দিয়েই, বাড়ির সামনের সিঁড়িতে বসে মামা মাটির উপর হাত দিয়ে বাড়ি দিতে থাকেন ‘মা মা’ বলে। মাত্র সতের বছরের বড় মা তাঁর। তাঁরা দুজন প্রায় একই সাথে বড় হওয়া। এত মানুষ কাঁদতে দেখে বাকি ছোটরাও কাঁদতে থাকে। আমি কেবল ঘুরে ঘুরে সবাইকে কাঁদতে দেখি। মুখস্থ করার মত আগ্রহভরে দেখি।
তারপর, বোল হরি হরি বোল। খাটিয়া তুলে নেয় ছেলেরা। তুলে নেওয়ার আগে পায়ে আলতা দেওয়া হয়, আলতা পায়ের ছাপ নেওয়া হয়। শ্মশান বাড়ির কাছেই, ওরা তুলে নিয়ে যাওয়া শুরু করে। বাড়ি থেকে শ্মশান কাছেই। আমাদের যেতে দেওয়া হয় না প্রথম। যখন বিকেলের দিকে, প্রায় পোড়ানো শেষ, তখন আমরাও যাই। আমি সেই প্রথম শ্মশানে যাওয়া। শ্মশানে তখন চিতা প্রায় নিভে নিভে গেছে। অস্থি নিয়ে বাড়ি ফেরার সময়। আমি, সাধনা বটব্যালের বহু আদরে তৈরি হওয়া প্রায়-আঁতেল নাতনী, তাঁরই চিতায় পুড়ে যাওয়ার দিন, ঘুরে ঘুরে আশেপাশের স্তম্ভে লেখা এপিটাফ পড়ি। পাশের এক স্তম্ভে একটা মেয়ের স্তম্ভ, ছবি নাম, তার জন্য একটা বড় কবিতা লেখা। “কোন পথে ছবি সেথা করিলে গমন”; ছোটো মেয়ে মারা গেছে, তার ভাইবোন কেউ লিখেছে – যেই পথে কেউ ফেরে না, কোন অভিমানে সেখানে গেলি তুই?
শ্মশান ব্যাপারটা আমার ভালোই লাগে দেখতে। কিছু বড় বড়, কিছু প্রায় মাটির ঢিবি স্তম্ভ। আসলে মরার পরেও তো ধনী- গরীব পার্থক্য যায় না মানুষের। যার যেমন টাকা, তার তেমন স্তম্ভ। আমার নাটুকে দিদিমা’র ইচ্ছা ছিল তাঁকে যেন নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয় মরে গেলে। মামা বলেন, মাটিচাপা দিতে বললে দিতাম। নদীতে ভাসিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা রাখাটা একটু বাড়াবাড়ি। কথাটায় যুক্তি আছে, আমার মনে হয়। কবিতা পড়লেই মুখস্থ থাকতো, ওইকালে। আমি ঘুরে ঘুরে শ্মশানের স্তম্ভে লেখা কবিতা মুখস্থ করতে থাকি।
বাংলাদেশে মৃত্যুও বড় অদ্ভুত ব্যাপার। অন্তত মধ্যবিত্ত ঘরে। শোক প্রকাশের বহু আগে ব্যবস্থা করতে হয় খাওয়াদাওয়ার। শ্রাদ্ধের আইটেম, কে রাঁধবে, কই খাওয়ানো হবে। কার্ড ছাপানো ইত্যাদি। এইসবই বাড়ির সামনের মাঠেই হয়। চারদিনের দিন মা’ও শ্রাদ্ধের কাজ করেন, বিবাহিত মেয়ের জন্য সেটাই নিয়ম। দিদিমা’র শ্রাদ্ধে দিদিমা’র পছন্দের আইটেম রাখার নিয়ম। এই নিয়ম মেনে রাখা হলো টমেটোর চাটনি। টমেটো তাঁর অনেক পছন্দের ছিল। টমেটো আমারও প্রিয়। দিদিমা যা যা খান না, আইড় মাছ, বোয়াল মাছ, ইত্যাদি আমিও খাই না। এরপর অনেক “ধুমধাম” হইচই এর মধ্যে ভাগ্যবতী সধবা সাধনা বটব্যালের মৃত্যুপরবর্তী শ্রাদ্ধকাজ সম্পন্ন হয়। বরিশালে এদের প্রায় সবাই চেনে, অনেক লোক আসে কাজে। বাংলাদেশে মানুষ মরে গেলে কেউ তার স্মৃতিচারণ করেনা, মানুষ এসে এসে বলে, “আমারও অমুক তমুকের ক্যান্সার হয়েছিলো, তারাও… ইত্যাদি”।
আমি শ্রাদ্ধকাজ দেখি, দেখাই একমাত্র কাজ যেটা আমি ঠিকঠাক পারি। পর্যবেক্ষণ বলা যায় আমার একমাত্র প্রতিভা। শেষের কয়দিন দিদিমা ঠিক মানুষের মত বেঁচে ছিলেন না, আর বাড়িভর্তি এত লোক, সবমিলিয়ে ঠিক দিদিমা’র অনুপস্থিতিও আকার নিচ্ছিল না। আজ, এতদিন পর, জানি যে, ওইদিনগুলো আমি ঠিক দিদিমা’কে মিস করছিলাম না। কিন্তু বাড়িতে যে ৬৪ টা মুরগি ছিল তাঁর, অসুস্থ হওয়ার আগে পর্যন্ত খেটে খাওয়া লোক ছিলেন তিনি – এই মুরগি না থাকাটা আমাকে কষ্ট দেয়। দিদিমা না, দিদিমা’র মুরগিগুলোর কথা আমি ভাবি ঘুরে ঘুরে। ওদের দিদিমা বিছানার নিচে একটা ঝাড়িতে এনে রাখতেন ডিমে তা দিতে। ডিম ফেটে ছোট ছোট মুরগি হলে আমি দেখতে যেতাম বারবার। দিদিমা না ঠিক, কিন্তু মুরগিগুলোর কথা ভেবে, আমার চোখে জল আসে। ওদের আর দেখবো না এইরকম একটা সিদ্ধান্ত পৌঁছাতে আমার দেরি হয় না।
দিদিমা যে নেই, আর যে আমাদের দেখা হবে না, এই কথাটুকু বুঝতে আমার আরও অনেকদিন লাগে। এই কথাটা হয়তো সত্যি বলে আমার কোনোদিন মেনে নেওয়া হবে না।
এর ছয় মাস পরে স্ট্রোকে দাদু দুইদিনের মধ্যে মারা যান। আমি ঢাকায় তখন, তাঁর মৃতদেহ আমি দেখিনি। পঞ্চাশ বছরের উপরের বিবাহিত জীবন শেষ হলে পর, “আমি আরেকটু ভালো ব্যবহার করতে পারতাম” হয়তো এই অনুশোচনাই তাঁকে আর বেশিদিন থাকতে দেয় না পৃথিবীতে। আমার হাতেখড়ি তাঁর হাতে। অনেক যত্নে তিনি আমাকে গ্রামারের জাহাজ বানাতে চেয়ে অসফল হয়েছিলেন। কিন্তু শিক্ষকতার প্রতি তাঁর ডেডিকেশনটা আজো মনে রয়ে গেছে। আজকাল ওই ধরনের শিক্ষক দেখা যায় না।
অপর্ণা হাওলাদার : পোস্টডক্টরাল ফেলো, ইউনিভার্সিটি অব রোড আইল্যান্ড, ইউএসএ